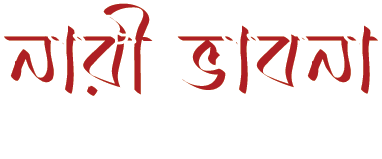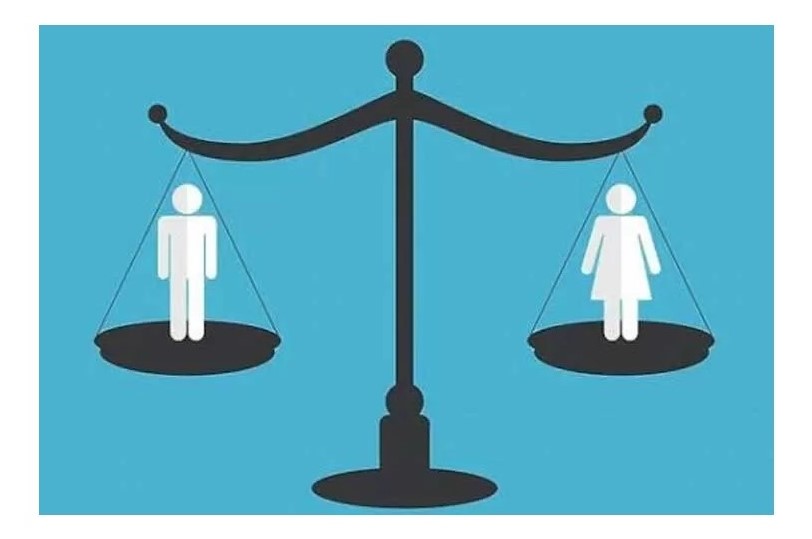পারিবারিক বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা থেকে যে আইন তাই পারিবারিক আইন নামে পরিচিত। পারিবারিক বিষয়াদি যেমন-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব নির্ধারণ ও উত্তরাধিকার বিষয়াদি এই আইনের অন্তর্ভুক্ত। আইন মূলত একটি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। আমাদের দেশের এই পারিবারিক আইন বৈষম্যমূলক । অন্যান্য দেওয়ানি – ফৌজদারি আইন নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক না হলেও এই পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনে বৈষম্য রয়েছে। কারণ আমরা যে রাষ্ট্রে বাস করছি তা একটি বৈষম্যমূলক রাষ্ট্র। এখানে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, ধর্মে- গোত্রে বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্যের কারণে যে বৈষম্যমূলক আইনের সৃষ্টি তার মূল উৎপাটনে কাজ করাই আমাদের লক্ষ্য।
বাংলাদেশের নারী সমাজকে প্রধানত দুইটি বিষয় সামনে রেখে লড়াই করতে হচ্ছে-
০১) পুরুষতান্ত্রিক মাসনসিকতা
০২) পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তি
পুরুষতান্ত্রিক মাসনিকতা হলো সেই পশ্চাৎপদতা দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে নারীকে প্রতিনিয়ত হেয় প্রতিপন্ন করে দেখা হয়। বিদ্যমান এই সমাজ প্রথা, রীতিনীতি, আইন-কানুন এবং প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে এই মানসিকতাকে টিকিয়ে রেখেছে। আর উৎপাদনের হাল-হাতিয়ার মালিক তার অধীনে রেখে পুঁজির শোষণকে টিকিয়ে রাখছে। ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এই শোষণের শিকার হলেও সমাজে নারীর অধঃস্তনতার কারণে নারীই বেশি শোষণের শিকার। তাই বাংলাদেশের নারীসমাজ সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করে অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইউনিফরম সিভিল কোড প্রতিষ্ঠার দাবি করে আসছে। ইউনিফরম সিভিল কোড হলো সেই আইন যা নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেই পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে নাগরিক হিসেবে একই অধিকার ভোগ করবে। নারী-বা পুরুষ ভেদে বা ধর্ম ভেদে আলাদা কোনো আইন থাকবে না। সবাই নাগরিক হিসেবে যার যে অধিকার সেটা ভোগ করবে।
আমরা সকলেই জানি, বাংলাদেশের এই পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন ধর্মীয়-বিধান থেকে এসেছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে এর পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধন হয়েছে। যেমন, ১৯৬১ সালের পূর্বে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে এতিম সন্তানরা বাবা-মা মারা গেলে পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ ও মাতামহীর সম্পত্তিতে অংশীদার হত না। কিস্তু ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে সম্পত্তিতে এতিম সন্তানদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়। হিন্দু সমাজে ‘বিধবা বিবাহ আইন’ ১৯৬৫ সালে পাস করা হয়। খ্রিস্টান ধর্মের আইনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু উত্তরাধিকার আইনে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরেও উপেক্ষিত।
নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যবিলোপ সনদ (সিডও) ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু এই সনদ স্বাক্ষর করার ৪১ বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত সিডও সনদের পূর্ণস্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন হয়নি। সিডও সনদের প্রাণ বলে খ্যাত দুটি ধারা ২ ও ১৬ (১ )(গ) সংরক্ষণ রেখে সরকার এটি স্বাক্ষর করেছে। কারণ অনুচ্ছেদ ২ এ নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য বিলোপ এবং ১৬(১) এ বিবাহ ও বিচ্ছেদকালে নারী এবং পুরুষের একই অধিকার এবং দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে । সিডও সনদের এই অনুচ্ছেদ সংরক্ষণ রেখে সরকার বিদ্যমান পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনের বৈষম্য বহাল রেখেছে। যেহেতু পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন ধর্মভিত্তিক সেজন্য নারীসমাজের পক্ষ থেকে সম্পত্তিসহ সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উঠলেও সরকার সেই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বার বার। প্রতিটি সরকার যেহেতু ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে সেজন্য বৈষম্যমূলক এই আইন পরিবর্তনে তারা কোন ভূমিকা পালন করে না। অথচ সংবিধানের ২৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা আছে – কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ -নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। কিন্তু পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের সুষ্পষ্ট লংঘন। বিদ্যমান এই উত্তরাধিকার আইন কিভাবে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা তা উত্তরাধিকার আইন পর্যালোচনা করলেই পাওয়া যাবে।
মুসলিম উত্তরাধিকার আইন
কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তার জীবিত আত্নীয়-স্বজনদের যে অধিকার জন্মায় তাকে উত্তরাধিকার বলে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের মূল উৎস কুরাআন হলেও বিভিন্ন সময়ে মুসলিম আইন বিশারদগণ তাদের অভিজ্ঞতার আলোক উত্তরাধিকার নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের ৩টি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-
১. জীবিত অবস্থায় যে কোন ব্যক্তির সম্পত্তিতে অন্য কারোর অধিকার জন্মায় না
২. যে কোন মুসলমান ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় তার সম্পত্তি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে
৩. কোন মুসলমান জীবিত অবস্থাতেই তার সম্পত্তি হস্তান্তর সম্বন্ধে নির্দেশ রেখে যেতে পারে যা তার মৃত্যুর পর কার্যকরি হয়। তাকে উইল বা অছিয়তনামা বলে।
উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের পূর্বশর্ত: একজন মুসলিম নারী বা পুরুষের মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টনের আগে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পালন করতে হবে
১. মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের খরচ পরিশোধ করা,
২. স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ করা,
৩. মৃত ব্যক্তির কোনো ঋণ বা দেনা থাকলে তা পরিশোধ করা,
৪. মৃত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো উইল করা থাকলে সেই উইলে উল্লেখিত সম্পত্তি প্রদান করা। এরপর যে সম্পত্তি থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন হবে।
মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তির উত্তরাধিকার: মুসলিম আইনের বিধানমতে উত্তরাধিকারীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়,
১. অংশীদার,
২. অবশিষ্টভোগী,
৩. দুরবর্তী আত্মীয়।
অংশীদারদের সম্পত্তি দেয়ার কিছু কিছু ব্যতিক্রম সাপেক্ষে অবশিষ্টভোগীরা সম্পত্তিতে অংশীদার হন। আর মৃত ব্যক্তির অংশীদার ও অবশিষ্ট ভোগী অংশীদার না থাকলে দুরবর্তী আত্মীয়গণ সম্পত্তি পান।
অংশীদার মোট বারোজন। তার মধ্যে আটজনই নারী । এর মধ্যে পাঁচজন প্রধান অংশীদার। এই পাঁচজন অংশীদার হলো (ক) পিতা (খ) মাতা (গ) স্ত্রী/স্বামী (ঘ) ছেলে (ঙ) মেয়ে। প্রধানত এই পাঁচজন উত্তরাধিকারীর মাঝে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টন হয়ে থাকে। এই পাঁচজন উত্তরাধিকারী বেঁচে থাকলে বাকীরা সম্পত্তি পায় না।
এতিম নাতি-নাতনীদের সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকার
১৯৬১ সালের পূর্বে প্রচলিত আইন অনুসারে এতিম নাতি-নাতনীরা তাদের নানা, নানী, দাদা বা দাদীর নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তি পেত না। ‘মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ’ ১৯৬১ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে বলবৎ হয়েছে এবং এখনও এই আইন বাংলাদেশে বলবৎ রয়েছে।
১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৪ ধারার মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, যার সম্পত্তি বন্টন হবে তার মৃত্যুর পূর্বে তার কোন পুত্র বা কন্যা মারা গিয়ে থাকলে এবং মৃত পুত্র/ কন্যা সন্তান জীবিত থাকলে সম্পত্তি বন্টনের সময় তার সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে, যা তাদের পিতা কিংবা মাতা বেঁচে থাকলে পেত। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির এতিম নাতি নাতনী থাকলে সম্পত্তি বন্টনের সময় তাদের বাবা-মাকে জীবিত মনে করে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্বে মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ তাদের পিতা মাতার স্থলাভিষিক্ত হবে, কিন্তু তাদের স্বামী বা স্ত্রী কিছুই পাবে না।
মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর সম্পত্তি:
কন্যা হিসাবে
– মৃত ব্যক্তির যদি একটি মাত্র কন্যা থাকে এবং কোন পুত্র না থাকে তাহলে কন্যা পিতার মোট সম্পত্তির অর্ধেক বা ১/২ অংশ পাবে
– মৃত ব্যক্তির যদি কোন পুত্র সন্তান না থাকে এবং দুই বা ততোধিক কন্যা থাকে তবে তারা সম্মিলিতভাবে মোট সম্পত্তির ২/৩ পাবে।
– মৃত ব্যক্তির কন্যার সাথে পুত্র থাকলে প্রত্যেক পুত্র কন্যার দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবে
স্ত্রী হিসাবে
– স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে দুইভাবে অংশ পান। প্রথমত যদি তাদের কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান না থাকে তাহলে স্ত্রী স্বামীর মোট সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবেন। দ্বিতীয়তঃ সন্তান থাকলে স্ত্রী মোট সম্পত্তির ১/৮ অংশ পাবেন। আবার যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকে তাহলে তারা ১/৪ অথবা ১/৮ অংশ নিজেদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে নেবেন।
– স্বামীও স্ত্রীর সম্পত্তিতে দুইভাবে অংশ পান। প্রথমতঃ যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে তবে স্বামী স্ত্রীর মোট সম্পত্তির ১/২ অংশ পাবেন
দ্বিতীয়তঃ যদি স্ত্রীর সন্তান থাকে তা ওই স্বামীরই হোক বা অন্য স্বামীরই বা তাদেরই সন্তান থাকে তবে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবে
মা হিসাবে
- মৃত্য ব্যক্তির কোনো সন্তান বা পুত্রের সন্তান থাকলে মা মোট সম্পত্তির ১/৬ অংশ পাবে
- যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান বা পুত্রের সন্তান না থাকে, একজনের বেশি ভাই বা বোন না থাকে তাহলে মা মোট সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবেন
- বোন হিসাবে
- মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী কেউ না থাকলে এবং শুধু একজন বোন থাকলে বোন অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।
- মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, পিতা, দাদা বেঁচে থাকলে বোন কোন সম্পত্তি পাবে না।
এখানে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কন্যা, স্ত্রী, মাতা ও বোন কেউই পিতা, স্বামী, ভাইয়ের সমান সম্পত্তি পায় না। আইনগতভাবে মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক সম্পত্তি পায়। আইনগত এই অধিকার থেকেও মেয়েদের বঞ্চিত করা হয়। আবার সমাজে এমন ধারণা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যে, যে সকল মেয়েরা সম্পত্তির অংশ নেয় তারা সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে নিচু স্তরের। মিথ্যা এই আভিজাত্যের কারণে বোনের সম্পত্তি সাধারণত ভাইয়েদের ভোগ দখলে চলে যায়। মাতাও ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তার সম্পত্তি ভাগের প্রশ্ন তোলেন না। এই কথাও প্রচলিত আছে যে, মেয়েরা বাবার কাছ থেকে সম্পত্তি পান আবার স্বামীর কাছ থেকেও সম্পত্তি পান। ফলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি সম্পত্তি পান। কিন্তু উল্লেখিত আলোচনাই দেখা গেল যে, কোন অবস্থায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি সম্পত্তি পান না। সর্বক্ষেত্রে নারীর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যখন পৃথিবীব্যাপী তোলপাড় তখন আমরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই করছি। ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়ন নীতিমালার সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল – উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ ও ভূমির উপর অধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ দেয়া হবে। অথচ ২০১১ সালের নারী উন্নয়ন নীতিমালায় উপার্জনের, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কোথায় সমান অধিকার আর কোথায় অর্জিত সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ! এভাবে প্রতিটি সরকারই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে নারীর সমমর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছে। নারী যখন পরিবার, সমাজ রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তখন উত্তরাধিকার আইনের এই বৈষম্য বিলোপ না করা নারীর প্রতি রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বিলোপ করে সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করাই হবে নারীর প্রতি রাষ্ট্রের যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।
হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর সম্পত্তি
বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার আইন দায়ভাগা আইন মতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এখানে আমরা উত্তরাধিকার আইনে হিন্দু নারীদের অবস্থান দেখবো।
দায়ভাগা আইনমতে উত্তরাধিকারদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়-
১. সপিন্ড -(মোট ৫৩ জন) এরা প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী।
২. সকুল্য -(মোট ৩৩ জন) এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী। এবং
৩. সমানোদক-(মোট ১৪৭ জন) এরা তৃতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী।
মৃত ব্যক্তির মোট উত্তরাধিকারীর সংখ্যা (৫৩+৩৩+১৪৭) = ২৩৩ জন।
উক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে সপিণ্ডরা কেউ থাকলে সকুল্যরা সম্পত্তি পাবে না , আবার সকুল্যরা থাকলে সমানোদকরা সম্পত্তি পাবে না। এক্ষেত্রে সপিণ্ডদের সংখ্যা ৫৩ জন, ফলে সকুল্য ও সমানোদকদের সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই সপিণ্ডদের আলোচনায় এখানে প্রধান বিবেচ্য। সপিণ্ড ৫৩ জনের মধ্যে নারী মাত্র পাঁচ জন, এরা হলেন-বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী।
সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন ১৯৩৭ পাশ হওয়ার পর বিধবা এক বা একাধিক হলে সকলে মিলে এক পুত্রের সমান সম্পত্তি জীবনসত্ত্বে ভোগ দখল করতে পারবেন। স্ত্রীর পরেই কন্যার দাবি। কন্যাদের মধ্যে প্রথমে অবিবাহিত কন্যা, এরপর ছেলে সন্তান আছে এমন কন্যারাই জীবনসত্ত্বে সম্পত্তি লাভ করবেন। যে সকল কন্যাদের সম্পত্তি নেই, যে সকল বিধবা কন্যাদের পুত্র সন্তান নেই, যে কন্যাদের শুধুমাত্র কন্যা সন্তান তারা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। এই আলোচনায় দেখা যায়, হিন্দু নারীরা উত্তরাধিকার সূত্রে কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্পত্তি পেলেও তা শুধু ভোগ করতে পারবেন কিন্তু বিক্রি, উইল, দান, স্বাধীনভাবে হস্তান্তর ইত্যাদি করতে পারেন না। শুধু মাত্র তিনি যার কাছ থেকে সম্পত্তি পেয়েছেন তার শ্রাদ্ধ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন।
স্ত্রীধন
স্ত্রীধন হলো, যে সম্পত্তিতে একজন নারীর পূর্ণ মালিকানা বা অধিকার রয়েছে অর্থাৎ যেসব সম্পত্তি নারীরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্রি, উইল, মালিকানা পরিবর্তন এবং ভোগদখল করতে পারে। এক কথায়, যেসব সম্পত্তিতে নারীরা সম্পূর্ণ স্বত্বের অধিকারী হয় সেই সব সম্পত্তিকেই স্ত্রীধন বলা হয়। স্ত্রীধন আলোচনার ক্ষেত্রে স্ত্রী বলতে কারো বিবাহিত মেয়ে বা যে কোন নারীকে বোঝানো হয়েছে।
স্ত্রীধন মালিকানা প্রাপ্তির উপায়সমূহ
একজন নারী যে সমস্ত উপায়ে স্ত্রীধনের মালিকানা প্রাপ্ত হন তা নিম্নে দেয়া হলো: যথা-
১. একজন নারী কুমারী, বিবাহিত অথবা বিধবা অবস্থায় উত্তরাধিকারসূত্র ব্যতীত অন্য যেকোনভাবে সম্পত্তির মালিক হলে সেই সব সম্পত্তিই স্ত্রীধন।
২. স্বামী-স্ত্রী পৃথক বসবাস থাকা অবস্থায় স্বামীর নিকট থেকে ভরণপোষণের জন্য প্রাপ্ত মাসোহারা দ্বারা অর্জিত সম্পত্তিও স্ত্রীধন হিসেবে গণ্য হবে।
৩. স্ত্রীধন দ্বারা অর্জিত সম্পত্তিও স্ত্রীধন।
উল্লেখিত উপায়ে প্রাপ্ত সম্পত্তি একজন নারী ইচ্ছানুযায়ী ভোগ, দখল, বিক্রি, উইল, দান ইত্যাদি করতে পারবেন। এছাড়া কোন নারী নিজে উপার্জন করে সম্পত্তি অর্জন করলে তা স্ত্রীধন হিসাবে গণ্য হবে।
হিন্দু আইনের সংস্কার
স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরেও এদেশে নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে একথা চরম-পরম সত্য । উল্লেখিত উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার চরমভাবে লংঘিত। নারীর সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব থাকলে তা শুধু ভোগদখলের জন্য। কারণ পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্জা- এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করাই হিন্দু আইনের মূল লক্ষ্য। অথচ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের হিন্দু পারিবারিক আইনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন-হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫, নাবালকের সম্পত্তি বিষয়ক আইন ১৯৫৬, হিন্দু দত্তক গ্রহণ ও ভরণপোষণ আইন ১৯৫৬, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯৫৬। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইনে এখনো সেই রক্ষণশীল প্রাচীন ধ্যানধারণাই রয়ে গেছে। হিন্দু পারিবারিক আইন পুরোপুরি নারী অধিকারের পরিপন্থী। তাই হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার এখন সময়ের দাবি।
খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনে নারী
বাংলাদেশের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উত্তরাধিকার নির্ধারণ হয় ১৯২৫ সালের সাকসেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী। কোন খ্রিস্টান নাগরিক মৃত্যু হলে তার সম্পত্তি সাকসেশন এ্যাক্টের ২৭ ধারায় নিয়মানুযায়ী ভাগ করা হয়। এই নিয়মগুলি উত্তরাধিকার নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য। নিয়মগুলো হল: –
১. উত্তরাধিকার হিসেবে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার।
২. পূর্ণরক্ত সর্ম্পক ও অর্ধ-রক্ত সর্ম্পকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই
৩. নিকটবর্তী আত্মীয় দুরবর্তী আত্মীয়কে প্রতিস্থাপিত করে
৪. মাতৃ-গর্ভের সন্তানও উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য হবে।
ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার জনগোষ্ঠির পারিবারিক আইন
বাংলাদেশে মোট ১৫টির মতো ক্ষুদ্রজাতি সত্ত্বার অবস্থান রয়েছে। চাকমা/মগ/খুমী/ এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। সাঁওতাল/রাজবংশী/খাশিয়া/ গারো/হাজং/সিন্ধা/হাদি/পলিয়া/মনিপুরী/ত্রিপুরা/ এরা মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। পরে এদের কেউ কেউ খ্রিস্টাান ধমর্ও গ্রহণ করেছে। এই ক্ষুদ্রজাতি সত্ত্বাসমুহের ধরা বাধা পারিবারিক আইন নেই। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই তাদের পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিশাল জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজন লিখিত পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন।
সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের এই যুগে এসে আমাদেরকে নারী-পুরুষের সমতা তথা উত্তরাধিকার আইনে সমতার দাবি উত্থাপন করতে হচ্ছে। কারণ উল্লেখিত আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে -ধর্মভিত্তিক উত্তরাধিকার আইনে নারী পুরুষের সমান অধিকার নেই। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তিতে নারীর অংশ বৈষম্যমূলক। কোনো বাবার যদি এক বা একাধিক কন্যা সন্তান থাকে তাহলে আইন অনুসারে বাবা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বে তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ কন্যা সন্তানকে দিতে পারবে না। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থান সবচেয়ে অবহেলিত। এখানে নারীর নিজস্ব অর্জিত সম্পত্তি বা উপহার সামগ্রী ছাড়া এক কথায় স্ত্রী-ধন ব্যতিত আর কোন সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব নারী পায় না। তবে খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তিতে নারী পুরুষের অধিকার প্রায় সমান।
মুসলিম প্রধান দেশ তুরস্ক, তিউনিশিয়াসহ আরো কয়েকটি দেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হিন্দু প্রধান দেশ ভারতে ধর্মীয় প্রথার অধিকাংশই বাতিল ও সংস্কার করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে যখনই উত্তরাধিকার আইনে পরিবর্তনের প্রশ্ন আসে তখনই সাম্প্রদায়িক শক্তি এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং আইন পরিবর্তনের বিরুদ্ধাচারণ করে। কোনো সরকারই এই আইন পরিবর্তনে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বরং রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও শক্তিসমুহহের কাছে মাথা নত করেছে।
রাষ্ট্রের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু উত্তরাধিকার আইনে এই পার্থক্য বিদ্যমান। তাই এই পার্থক্য দূরীকরণে উত্তরাধিকার আইনসমূহকেও দেওয়ানী আইন ও আদালতের আওতায় এনে ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রবর্তন করে উত্তরাধিকার আইনের বৈষম্য দূর করতে হবে। ফলে সরকার যদি সিডও সনদ, সংবিধান এবং অন্যান্য আর্ন্তজাতিক আইনের আলোকে সমাজে বিরাজমান বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে তাহলে সমাজে নারীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি আছে তার পরিবর্তন ঘটবে।
তথ্যসূত্র:
১. পারিবারিক আইনে বাংলাদেশের নারী- আইন ও সালিশ কেন্দ্র
২. নারী বিষয়ক আইন-কানুন – মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান ও মোঃ মতিউল ইসলাম সম্পাদ্দিত
৩. নারী অধিকার ও কয়েকটি আইন – তাহমিনা হক
লেখক
মোছাঃ মর্জিনা খাতুন, নারী অধিকার কর্মী