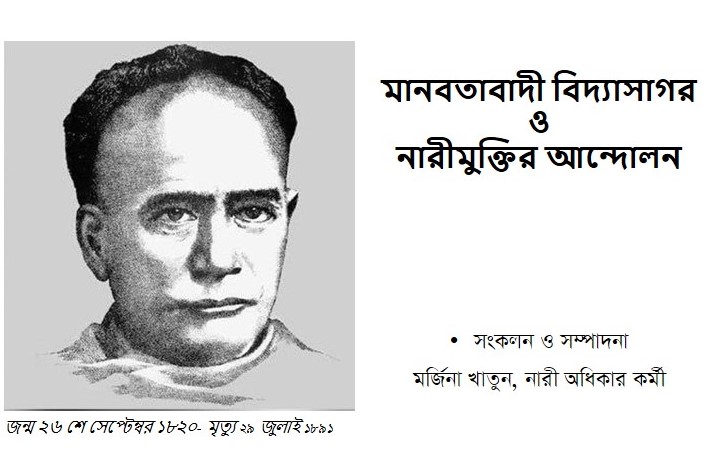ইউরোপে যখন মানবতাবাদের উম্মেষ ঘটেছে তখন মানবতাবাদ ছিল বিকাশমান, আপোসহীন। মানবতাবাদ তখন সামন্তসমাজকে ভেঙ্গে এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। ব্যক্তিকে ঈশ্বর ও রাজার নিরঙ্কুশ আধিপত্য থেকেও মুক্ত করতে চেয়েছে। ভারতবর্ষে যখন মানবতাবাদের বিকাশ ঘটেছে তখন বিশ্বে পুঁজিবাদ কয়েক শতক পার করে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে উপনিবেশ স্থাপনের পথে পা বাড়িয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। ফলে ভারতবর্ষে মানবতাবাদের বিকাশ আপোষমুখী পথে হয়েছে। সে কারণে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রী-গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বিকাশ শুরু থেকেই হয়ে পড়েছে আপসমুখী। এই আপোসমুখী পথে ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজা রামমোহন রায় ভারতে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটালেন। ধর্মের সংগে মিলিয়ে সংস্কারপন্থী পথে নবজাগরণের যে ধারা ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়েছিল বিদ্যাসাগরের পার্থিব মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার সম্পূর্ন বিপরীত। সমগ্র সমাজের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর একা দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিলেন। যুক্তি ও বিজ্ঞান ছিল তাঁর লড়াইয়ের প্রধান হাতিয়ার। এর ভিত্তিতে তিনি বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিগত চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন।
সাধারণভাবে বিদ্যাসাগরকে আমরা চিনি দয়ার সাগর, করুণাসাগর রূপে। বিদ্যাসাগর মানুষ কেমন ছিলেন-বলতে গেলেই আমরা বলি দীন-দুঃখী-অসহায় মানুষ, বিশেষ করে বিধবা বা কৌলিণ্য প্রথার বলি বাল-বধুদের প্রতি তাঁর করুণাকোমল, দয়াপ্রবণ, দানশীল চরিত্রের কথা । আর এই চরিত্র গড়ে উঠার পেছনে ভূমিকা পালন করেছে তাঁর ¯স্নেহশীলা মায়ের প্রভাব; যে মায়ের প্রতি বিদ্যাসাগরের ভক্তি-ভালোবাসা এদেশে প্রায় প্রবাদের মত। আবার একই সঙ্গে আমরা স্বীকার করি যে এক প্রচন্ড তেজ, প্রগাঢ় মর্যাদাবোধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। চরিত্রের দৃঢ়তা তিনি পেয়েছেন পিতা ঠাকুরদাস বা পিতামহ রামজয় তর্কভুষণের তেজস্বিতা থেকে। তেজস্বি মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর।
বিদ্যাসাগরের চরিত্রে মা ভগবতী দেবীর প্রভাব: বিদ্যাসাগরের চরিত্র গড়ে উঠার পিছনে তাঁর মা ভগবতী দেবী’র প্রভাব ছিল অসীম। বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন, “আমি যদি আমার মায়ের গুণের একশো ভাগের এক ভাগও পেতাম, তাহলে কৃতার্থ হতাম। আমি যে অমন মায়ের সন্তান এই আমার গৌরব। (মা ও ছেলে; প্রথম ভাগঃ চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭৭) ভগবতী দেবী শুধু একজন ¯স্নেহশীলা মা-ই ছিলেন না, হিন্দু ব্রাক্ষ্ন বধু হয়েও তাঁর ছিল এক সংস্কার-মুক্ত মন, নিলোর্ভ, নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র। তখনকার দিনে আত্মীয়স্বজনের ভ্রæকুটি উপেক্ষা করে, বাড়িতে আশ্রিতা বা অতিথি বিধবাদের সঙ্গে তিনি একপাতে খেতেন।
একবার বীরসিংহের বাড়ি পুড়ে গেলে বিদ্যাসাগর মা-কে কলকাতায় নিয়ে যেতে চান। ভগবতী দেবীর জবাব ছিল- “যেসব গরীবের ছেলে এখানে খেয়ে বীরসিংহ ইস্কুলে পড়ে, আমি এখান থেকে চলে গেলে তারা কী খেয়ে ইস্কুলে যাবে?” বিদ্যাসাগর একবার মাকে গহনা দিতে চান। ভগবতী দেবী জানান, “বাবা অনেকদিন থেকে আমার তিনখানি গহনা পরবার বড় ইচ্ছা আছে। ১. গ্রামের ছেলেদের জন্য একটি দাতব্য বিদ্যালয় করে দাও, ২. গ্রামের গরীব মানুষদের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করে দাও, ৩.আর গ্রামের গরীব ছেলেদের থাকা-খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দাও। অনেকদিন ধরে আমার এই তিন গহনার বড়ো ইচ্ছা।” (বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবীঃ প্রিয়দর্শন হালদার, পৃষ্ঠা ১১২-১৩)। ভগবতী দেবীর এই ছিল গহনার বর্ণনা।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তেমন মায়ের একজন সন্তান। সংস্কৃত কলেজের নানাবিধ কাজের মধ্যে তীব্র সমাজ সংগ্রামে ব্যাপৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁর মা কাঁদতে কাঁদতে এসে এক ছোট্ট বালিকার বৈধব্যের কথা বলে বললেন, ‘এত দিন এত শাস্ত্র পড়লি, তাহাতে বিধবার কি কোন উপায় নেই?’ মায়ের এই কথা বিদ্যাসাগরের মনে শেল সম বিদ্ধ করেছিল। তাই সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীর আশ্রয় নিয়ে রাশি রাশি হস্তলিখিত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। অনেক অনুসন্ধানের পর বিধবার পুনবির্বাহ দেয়ার শাস্ত্রীয় বচন পেলেন, তখন তিনি মায়ের চরণ বন্দনা করে বললেন-“ মা শাস্ত্রের বচন পাইয়াছি এখন বিধবার বিবাহ দিতে হইবে, তুমি কি বল? পুত্রবৎসল মা পুত্রকে উৎসাহ দিয়ে কার্যে প্রবৃত্ত করলেন।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরর ছোট ভাই শম্ভচন্দ্র বিদ্যারত্ন মা ও ছেলের যৌথ কাজের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন:‘১২৬৬ সাল হইতে ১২৭২ সাল পর্যন্ত (১৮৬০-১৮৬৬) ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজ মহাশয় বিশেষরূপে যতœবান ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপনার দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিত ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে, এ কারণে জননী দেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রা²ণ জাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্রে এক পাত্রে ভোজন করিতেন।’
মা ও ছেলের এই সংগ্রাম তৎকালীন সময়ে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পিতা ঠাকুরদাসকেও বিদ্যাসাগর প্রভূত শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর প্রভাবও বিদ্যাসাগরের উপর পড়েছিল।
শুধু পরিবার নয় সমাজের বাস্তব পরিস্থিতিও বিদ্যাসাগরের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। কারণ কোনও মানুষের চরিত্র কখনও তার সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠে না; ব্যক্তির প্রভাব কাজ করলেও, তার মূল প্রোথিত থাকে সমাজের বাস্তব অবস্থার বুনিয়াদের মধ্যে। ধর্মীয় প্রভাব আর বৃটিশ শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট সমাজের অভ্যন্তরে যে অন্যায়, অবিচার, অশিক্ষা, অহাসয়তা সাধারণ দরিদ্র মানুষকে গ্রাস করে রেখেছিল তাঁর বিরুদ্ধে সমাজে যে জাগরণ সেদিন হয়েছিল তাই ছিল তখনকার প্রগতিশীল চিন্তা বা মানবদরদ। বিদ্যাসাগর স্বীয় জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তখনকার সেই প্রগতিশীল চিন্তাকে ধারণ করতে পেরেছিলেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে ধারণ করতে পেরেছিলেন। ফলে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে উঠেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিসাবে।
মানবদরদী বিদ্যাসাগর: বিদ্যাসাগর মানবদরদী ছিলেন, তাঁর সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম-ব্যক্তিগত তথা সামাজিক-সবকিছুরেই কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ, যেখানেই তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, অশিক্ষা-অসহায়তা দেখেছেন, তাঁর প্রাণ শুধু কেঁদে উঠেনি, যথাসাধ্য এমন কি সাধ্যাতীত সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছেন। মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁর জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, এমনকি অন্যের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে মধুসূদনকে দিয়েছেন, তেমনই এক প্রতিবেশীর কলেরা রোগগ্রস্থ পরিচারককে রাস্তা থেকে তুলে এনে নিজের বাড়িতে রেখে শুশ্রƒষা করেছেন; ছোট-বড়-উঁচু-নীচু, হিন্দু-মুসলমান, ব্রা²ণ-ডোম কোনও পরিচয়ের প্রশ্ন আসেনি। তাই বাঙালির ইতিহাস লিখতে গিয়ে সব ধর্মের মানুষরাই সমানভাবে স্থান পেয়েছেন তাঁর লেখনিতে। ডোমের বস্তিতে কলেরার প্রকোপ দেখে উপবীত-ধারণ করা ব্রা²ণ পÐিত ছুটে গিয়েছেন রোগীর সেবা করতে; কার্মাটার সাঁওতাল পল্লীতে সরলমনা, সত্যবাদী সাঁওতালদের মাঝে গিয়ে মহা আনন্দে কাটিয়েছেন।
আবার এদেশে শিক্ষার আধুনিক কার্যক্রম গড়ে তোলার প্রশ্নে নিদ্বিধায় ঘোষণা করেছেন “ সাংখ্য- বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন”-পরিবতের্ তাঁর সুষ্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব ফুটে উঠেছে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি; শিশুদের জন্য জীবনচরিত্র রচনা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে নীতিবোধ, চরিত্রে মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধের বীজ বপন করতে -বিদ্যাসাগর কোনও ধর্মীয় মহাপুরুষের জীবনীর কথা লিখেননি, লিখেছেন নিউটন-গ্যালিলিও’র মত বিজ্ঞানীর জীবনী। আজীবন সংগ্রাম করে যাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তেমন মানুষের কথা। ফলে শুধু নবজাগরণের মানবতাবাদ-ই নয়, বিদ্যাসাগর হয়ে উঠেছেন এদেশে পার্থিব মানবতাবাদের প্রবক্তা। বিদ্যাসাগরের সমস্ত মূল্যবোধ এই মানবতাবাদকেই ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। শুধু মানবদরদ-ই নয়, বিজ্ঞানচেতনা, ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।
বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে সমাজে শ্রম-বিভাজনও ঘটত ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী। সমাজের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, সুবিধাভোগী পুরোহিত-রাজা-সামন্ত প্রভুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল বিশেষ কাজ। আর যত কায়িক শ্রম, তথাকথিত “ছোট” কাজের দায়িত্ব ছিল নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের হাতে। আবার স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও ছিল নির্দিষ্ট শ্রম-বিভাজন। বুর্জোয়া সমাজে মানুষে মানুষে সাম্যের চিন্তার পরিপূরক হিসাবেই আসে শ্রমের মর্যাদাবোধের চিন্তা, স্ত্রী-পুরুষ, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল শ্রমে সকলের সমান অধিকার ও দায়িত্বের মূলবোধ। ব্যক্তি জীবনে বিদ্যাসাগর এই মূল্যবোধকে যে কত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার অজস্্র উদাহরণ পাওয়া যায়। কুলির খোঁজে ব্যস্ত বাবুর মাল বহন করেছেন, বাগানের মাটি কোপিয়েছেন, আবার বাড়িতে অতিথিকে স্বহস্তে রান্না করে খাইয়েছেন, ছাত্রাবস্থায় কলকাতার বাসায় সকলের জন্য রান্না করে, গৃহস্থালীর কাজ সেরে পড়তে বসেছেন। আর যে কাজই করুণ, সংশ্লিষ্ট সকলেই সেই কাজের প্রশংসা করেছে তাঁর যতœ ও নিষ্ঠার সাথে নিখুঁত করে কাজটি করার মনোভাবের জন্য।
ব্যক্তিগত জীবনের চিন্তাদর্শ, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি কোন্ দর্শন অনুযায়ী তাঁর লক্ষ্য তথা কার্যক্রমকে পরিচালিত করেছেন-তা তাঁর কথার চেয়ে কাজের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে বেশি। প্রগাঢ় মানবদরদ থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিদ্যাসাগর অসহায় নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-শিশুকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন; কেন তাদের অসহায়তা, কেন তাদের অশিক্ষা, কি উপায়ে তাদের প্রকৃত শিক্ষিত করে তোলা যায়, কোন্ যুক্তিতে সমাজ বিধবাদের অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে ফেলে রেখেছে, তা থেকে তাদের মুক্ত করতে গেলে করণীয় কি-ইত্যাদি সব প্রশ্নেরই মীমাংসা করেছেন প্রখর যুক্তিবাদী চিন্তার সাহায্যে; ধর্ম ও ঈশ্বর ভক্তি, অন্ধ বিশ্বাসকে তীক্ষè আঘাত করেছেন যুক্তির বাণে; এই পথেই তাকে আমারা চিনে নিতে পেরেছি একজন বিজ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর মানবতাদী রূপে। আর তাঁর এই চিন্তাকে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা, কোনও বিপত্তি-ই তাঁকে নিবৃত্ত করতে পরেনি। একমাত্র লক্ষ্য উপলব্ধ সত্যকে, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা। আজীবন এই সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সমাজের মূলে আঘাত করেছেন, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।
শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি: সমাজ থেকে কুসংস্কার, পুরাতন ধ্যান-ধারণা দূর করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। সেই শিক্ষাকে তিনি সেকুল্যার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেখেছেন। একই সাথে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই বাংলা ভাষাকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ঘরে ঘরে শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা, বর্ণপরিচয় রচনা ও বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ করে বাংলা ভাষাকে উন্নত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে ইংরেজির সাথে সংস্কৃতের চর্চাও করতে হবে, না করলে বাংলা ভাষার বিকাশ হবে না। কারণ, সংস্কৃত হলো বাংলা ভাষার ভিত্তি। আবার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি আয়ত্ত করতে হয় তাহলে সেটা সংস্কৃত দ্বারা হবে না। সেজন্য ইংরেজি শিখতে হবে।” শিক্ষা থেকে তিনি সচেতনভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে বাদ দিয়েছেন। তিনি সাংখ্য-বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছেন। তিনি বলেছেন, পাঁচটা দর্শনের মতো সাংখ্য-বেদান্ত পড়তে হবে। এই দর্শনকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে পড়লে চলবে না। তাতে তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি বলেছেন যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ‘মিল’ এর লজিক পড়তে হবে। অর্থ্যাৎ অন্ধ বিশ্বাসের বিপরীতে তিনি যুক্তিবাদী মন, বিজ্ঞানমস্কতা ইত্যাদি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আনার চেষ্টা করেছেন।
বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলনে বিদ্যাসাগর : বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের এক বাল্য সহচরী ছিল। খুব অল্প বয়সে তার বিয়ে হয় এবং বিয়ের কয়েকমাস পরে সে বিধবা হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩/১৪ বছর। একদিন বিদ্যাসাগর খবর পেলেন তাঁর প্রতিবেশি সহচরী কিছু খায়নি, কারণ ঐদিন একাদশী। শুনে বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেলে বল্লেন একদিন তোদের দুঃখ দূর করবো। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। বিধবা নারীর জীবন যন্ত্রণা নিরসনের কোন পথ আছে কিনা তা জানবার জন্য দিনের পর দিন পুঁথির পাতায় পাতায় খুঁজেছেন, বহুদিন গেছে তিনি রাতে ঘুমাতেন না। আদ্যোপান্ত শাস্ত্র ঘেঁটে, শাস্ত্রেরই যুক্তিতে শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতদের ঘায়েল করেছেন, সমাজের অভ্যন্তরে জনমত সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, তারপর বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করার সময় অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন এবং এই বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকে তিনি নিজে জীবনের সৎকর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থ্যাৎ কঠোর প্রতিকূল পরিস্থিতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে দৃঢ়চিত্তে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।
তিনি বলেছেন,“তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না। দুর্জয় রিপুবর্গ একেবারে নির্মূল হইয়া যায় …… যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নেই…… কেবল লৌকিকতা রক্ষাই প্রধান ধর্ম ও পরম ধর্ম। আর যেন সেদেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না! ” (বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় পুুস্তুক, বিদ্যাসাগর রচনাবলী পৃষ্ঠা-৮৩৯)
এভাবে সমাজের কদর্য অনাচারের স্বরূপ উ˜্ঘাটন করে তিনি সোচ্চার হলেন বিধবা বিবাহের আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে। ১৮৫৫ সারের ৪ অক্টোবর তাঁর উদ্যোগে ৯৮৬ ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ বিধবা বিবাহ আইনের সমর্থনে এক আবেদন সরকারের নিকট পেশ করলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আরো বহু ব্যক্তির আবেদন সরকারের কাছে পৌঁছতে থাকে। ১৮৫৫ সালের ১৭ নভেম্বর আইন পরিষদে বিধবা বিবাহের পক্ষে আইনের খসড়া পেশ করা হয়। ১৮৫৬ সালে আবার এই খসড়া আইনটি দ্বিতীয়বার পেশ করা হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও জোর প্রতিবাদ উঠতে থাকে। প্রতিবাদ সত্তে¡ও ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহের আইন পাশ হয়।
এই আইন পাশের পর বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি গ্রামে-গঞ্জে ঘুরেছেন, বিধবার বিয়ে দিয়েছেন। ৭ ডিসেম্বর প্রথম বিধবা বিবাহ হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত¡াবধানে। এই বিধবা মেয়েটির নাম কালীমতী। মাত্র চার বছর বয়সে বিয়ে ও ছয় বছর বয়সে বিধবা হয়ে কালীমতী তখন ১০ বছরের বালিকা মাত্র। কিন্তু বৈধব্য জীবনের নানাবিধ বিধি-নিষেধের ফলে ওই বালিকা বয়সেই তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কালীমতীর বিয়ে হলো মুর্শিদাবাদের জজপন্ডিত সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র শ্রীশচন্দ্র (বন্দোপাধ্যায়) বিদ্যারতেœর সঙ্গে। এই বিয়ের খরচ বাবদ ১০ হাজার টাকার ব্যয়ভার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহন করেছিলেন। সে সময়ের বহু গুণীজন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, ‘তর্করত্ন’, ‘বিদ্যারত্ন’ ও ‘ন্যায়রত্ন’ উপাধিতে ভূষিত পন্ডিতবর্গ এই বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন।
১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত মাত্র ১১ বছর সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৬০ টি বিধবা বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এসব বিয়ের খরচ বাবদ ৮২ হাজার টাকার দায়িত্ব তিনি নিজে বহন করেছিলেন। এজন্য ৫০ হাজার টাকা ঋণ হয়েছিল। এই ঋণের কথা শুনে তাঁকে ঋণমুক্ত করার জন্য হিন্দু পেট্রিয়ট ও এডুকেশন গেজেট -এর সম্পাদকবৃন্দ এবং অন্য কয়েকজন ব্যক্তি ‘বিধবা বিবাহ তহবিল’ খোলার উদ্যোগ নিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আপত্তি জানান। সে জন্য সে উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজেই সেই ঋণ পরিশোধ করেছিলেন।
তিনি একজন সমাজকর্মী রূপে, নেতা রূপে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য আন্দোলন করেছেন। তাঁর পুত্র নারায়নচন্দ্র ১৮৭০ সালে জনৈকা বিধবাকে বিবাহের উদ্যোগ নিলে তিনি তা সমর্থন করেন। এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য আতœীয়স্বজনের বিরোধ বাধে। তখন তিনি বলেন, ’ আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি। এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না।’ এই ছিল বিদ্যাসাগরের উপলব্ধি ও ন্যায়বোধ। আবার সেই সন্তান পরে যখন আদর্শ ভ্রষ্ট হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে তখন সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন।
এই বিধবা বিবাহ দেয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই বিদ্যাসাগরকে বারণ করেছেন, তখন তিনি বলেছেন, “আমি দেশাচারের দাস নই, সমাজের মঙ্গলের জন্য যা করা উচিত তা করবো।” বিধবা বিবাহ প্রবর্তন হওয়ার পর একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যাসাগর রাস্তায় বের হলে তাঁকে ঘিরে ফেলতো, গালিগালাজ দিত, ঠাট্টা করতো, মেরে ফেলার হুমকি দিত, কিন্তু দৃঢ়চেতা বিদ্যাসাগর বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। বিধবা বিবাহ আইনস্মমত হলেও বিধবা নারীর প্রতি সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন এখনো হয়নি। এখনো সমাজে বিধবারা অবহেলিত, নির্যাতিত এবং অধিকার বঞ্চিত।
বাল্যবিবাহ রোধে বিদ্যাসাগরঃ বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ রোধের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমুধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখনও আস্বাদ করিতে পায় না, সুতারাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহকরণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। …..সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য তাহাও বাল্য পরিণয়যুক্ত ক্ষয় পায়। ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অম্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মূখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই। …..এতদ্দেশে পিতা-মাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ং বা অন্য দ্বারা পাত্র অন্বেষণ করিয়া, কেবল অসার কৌলিণ্য মর্যাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রাপ্তবিবাহকাল এবং অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করেন, উত্তরকালে কন্যার ভাবি সুখ-দুঃখের প্রতি একবার নেত্রপাত করেন না।”
অথ্যাৎ বাল্যবিবাহের ফলে পারিবারিক কলহ, সন্তানের অপ্রশস্ততা, নারীর শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যতার বিষয়ে বিদ্যাসাগর যে অকাট্য যুক্তি প্রদান করেছেন সেই যুক্তি আজও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ১২৯ বছর পরও বাল্যবিবাহ বন্ধের দাবিতে আমরা আন্দোলন করছি। এখনও আমাদের দেশে ৬৫ শতাংশ মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার। আবার তিনি সেই যুগেই ভেবেছিলেন, “মনের মিলই প্রণয়ের মূল।” মনের মিল ব্যতিত দাম্পত্য জীবন যে কত করুণ বর্তমান সমাজের পরিবারগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে তার প্রমাণ মেলে।
বহুবিবাহ রোধে বিদ্যাসাগরঃ ভারতবর্ষে স্ত্রী পুরুষের অধীন। ফলে পুরুষ নারীদের অবনত করে রাখত। সেই কারণে পুরুষ তার ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রীর উপর অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ করতো। পুরুষের এই অন্যায় আচরণ স্ত্রী সহ্য করত। পুরুষের নৃশংসতা, স্বার্থপরতা ও অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের কারণে স্ত্রীর যে অবস্থা ভারতবর্ষে হত পৃথিবীর অন্যকোন দেশে তা হতো কিনা সন্দেহ। পুরুষের অবিমৃশ্যকারিতার একটি বড় উদাহরণ হলো বহুবিবাহ। এই বহুবিবাহ স্ত্রীর জীবনে অশেষ যন্ত্রণার কারণ ছিল। এই বহুবিবাহ বন্ধে বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিদীর্ণ হতো। তাই বহুবিবাহ বন্ধে বিদ্যাসাগর সমাজে কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।
উল্লেখিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেদিন শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত মানুষকে যুক্ত করার উদ্দেশে একটি অঙ্গিকার পত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন। সেই অঙ্গিকার পত্রে ১০টি অঙ্গিকার লিপিবদ্ধ ছিল-
(১)কন্যাকে শিক্ষাদান করাইব। (২) একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে (কন্যার) বিবাহ দিব না। (৩) কুলীন, বংশজ, ক্ষেত্রিয় অথবা মৌলিক ইত্যাদি গনণা না করিয়া স্বজাতি সৎপাত্রে কন্যা দান করিব। (৪) কন্যা বিধবা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকলে, পুনরায় বিবাহ দিব। (৫) অষ্টাদশ বর্ষ পুর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না। (৬) এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে আর বিবাহ করিব না। (৭) যাহার এক স্ত্রী বিদ্যমান আছে, তাহাকে কন্যা দান করিব না। (৮) যেই রূপ আচরণ করিলে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধিও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, তাহা করিব না। (৯) মাসে মাসে স্ব স্ব মাসিক আয়ের অংশ ধনাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিব। (১০) এই প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিয়া কোন কারণে উপরি নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা পালনে পরাক্সমুখ হইবনা।
উল্লেখিত অঙ্গীকার পত্রই প্রমাণ করে কি সাহস, তেজ নিয়ে তিনি সেইদিন নারীদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আর এই আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁর নামে নিন্দার ঝড় উঠেছিল। কিন্তু এই আন্দোলন থেকে তিনি বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। জীবনের শেষ পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন।
নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর:নারী শিক্ষা বিস্তার বিদ্যাসাগরের অন্যতম কীর্তি। মেয়েরা পড়াশোনা করলে বিধবা হবে- সেজন্য তৎকালীন সমাজে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানো হত না। তিনি সমাজের এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নারীশিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হলেন। তাঁর আগেই নারীশিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হয়েছিল-বিশেষত উচ্চ স্তরের হিন্দু সমাজে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই একটি দুইটি করে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। ১৮৪৭ সালে বারাসাতে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর উদ্যোগে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তারপর ১৮৪৭ সালে কলকাতায় ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়, যা পরবর্তীতে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত হয়।
বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সাল থেকেই বেথুন স্কুলের পরিচালনা কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ সালে তিনি এই কলেজের নতুন ম্যানেজিং কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ সালে ছোট লাট হ্যালিডে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কাজে উদ্যোগী হন। তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর নিজের উদ্যোগে বর্ধমান জেলায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য সরকারি সাহায্যও মঞ্জুর হয়। সরকারের অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করেই ১৮৫৮ সালের মধ্যেই তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এর জন্য পরবর্তীতে নানা অসুবিধার মধ্যেও তাকে পড়তে হয়েছিল। সরকার এই বিদ্যালয়গুলোর জন্য সরকারি সাহায্য দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। তিনি স্কুলগুলো পরিচালনার জন্য “নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাÐার” খোলেন। এই প্রতিষ্ঠানে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিরা নিয়মিত চাঁদা দিতেন। এইভাবে সরকারের মূখাপেক্ষী না হয়েও বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি আরও বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের বুঝিয়ে মেয়েদেরকে স্কুলে আনতেন আবার বাড়ি পৌঁছে দিতেন। কারণ শিক্ষা ছাড়া সমাজ থেকে কুসংস্কার, অন্ধতা ও গোঁড়ামি দূর করা সম্ভব হবে না এই সত্যকে উপলব্ধি করেই তিনি আজীবন নারী শিক্ষা বিস্তারে প্রাণপন চেষ্টা করেছেন।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমস্ত চিন্তা ছিল মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই সমগ্র মানুষের প্রতি দরদবোধ বিশেষত নারী সমাজের মুক্তির আন্দোলনে তাঁর যে ভূমিকা তা অতুলীয়। তাঁর সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে করে তুলেছিল অনন্য। সত্যকে ধারণ করে একাকী দৃঢ়চিত্তে তিনি নারীর অগ্রগগিতে যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন আজও নারীমুক্তির আন্দোলনে তা পথপ্রদর্শক হয়ে আছে। আজকের যুগে নারীমুক্তির আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে সমাজের সমস্ত প্রতিকূলতা, অন্যায়-অত্যাচার, কূপমÐূকতা-কূসংসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দৃঢ়চিত্তে নারীসমাজকে জাগতে হবে। তবেই নারীমুক্তির পথ প্রশস্ত হবে। বিদ্যাসাগর যেমন করে সমাজের সমস্ত বেদনাকে বুকে ধারণ করেছেন তেমনি করে নারী আন্দোলনের কর্মীদেরকেও আজকের সমাজের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে যেমন দাঁড়াতে হবে তেমনি নিজের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিবেদিত হতে হবে। আপোষহীন, দৃঢ়চিত্ত, মানবদরদী ও সেকুল্যার চিন্তার বিদ্যাসাগর এই শিক্ষাই আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন। মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালের ২৯ শে জুলাই বিহারের কার্মাটারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও শুধু ভারতবর্ষে নয় সমগ্র পৃথিবীতে অগ্রগন্য মানবতাবাদী ও নারীমুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন।
সংকলন ও সম্পাদনা
মর্জিনা খাতুন, নারী অধিকার কর্মী
বি.দ্রষ্টব্য: আমার এই সংকলিত ও সম্পাদিত লেখাটি নারী চেতনা’র মার্চ 2016 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখাটিকে কিছুটা পরিমার্জন ও সংযোজন করে ‘নারী ভাবনা’ ব্লগে প্রকাশ করলাম।
তথ্যসূত্র:
- সেকুল্যার মানবতাবাদ ও বিদ্যাসাগর-শিবদাস ঘোষ, দি গোল্ডেন বুক অব বিদ্যাসাগর
- নবপর্যায়-জিজ্ঞাসা-বিদ্যাসাগর বিশেষ সংখ্যা-একত্রিংশ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা (২০১৩-২০১৪)
- পথিকৃৎ-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশেষ সংখ্যা, ঊনত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (অক্টোবর, ১৯৯১)
- নারী সংহতি- সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ২০১৩ এবং অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০১৪
- বাংলার নারী আন্দোলন – মালেকা বেগম